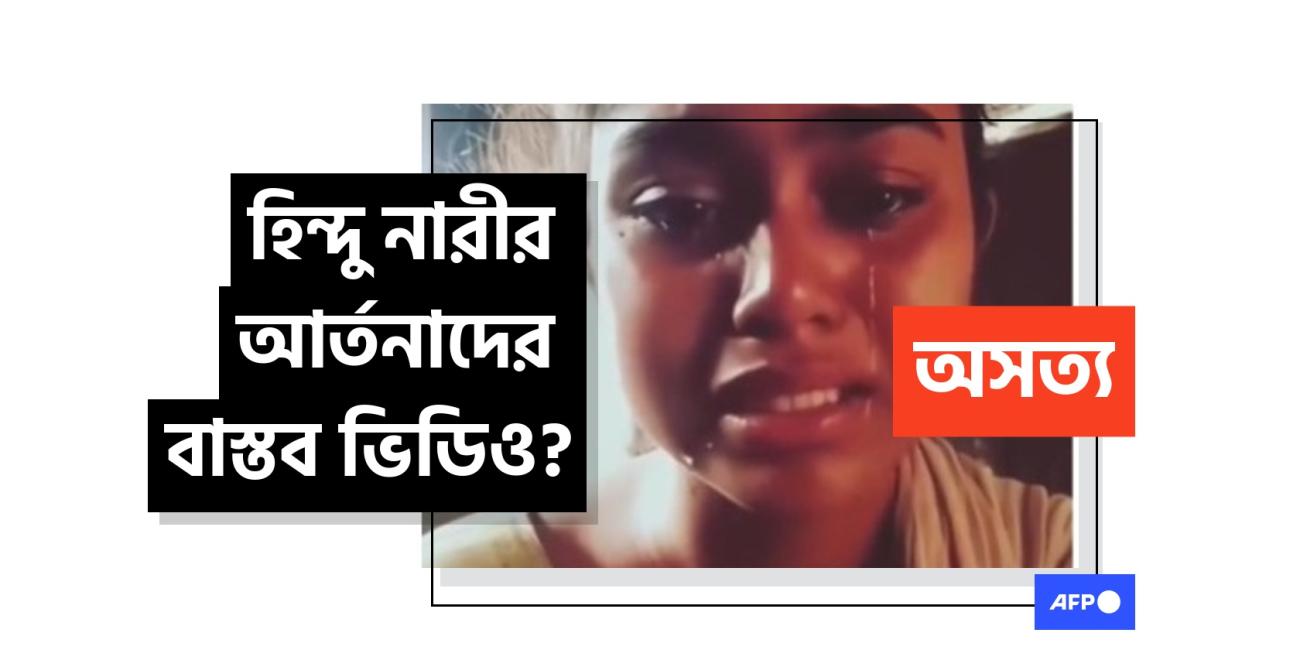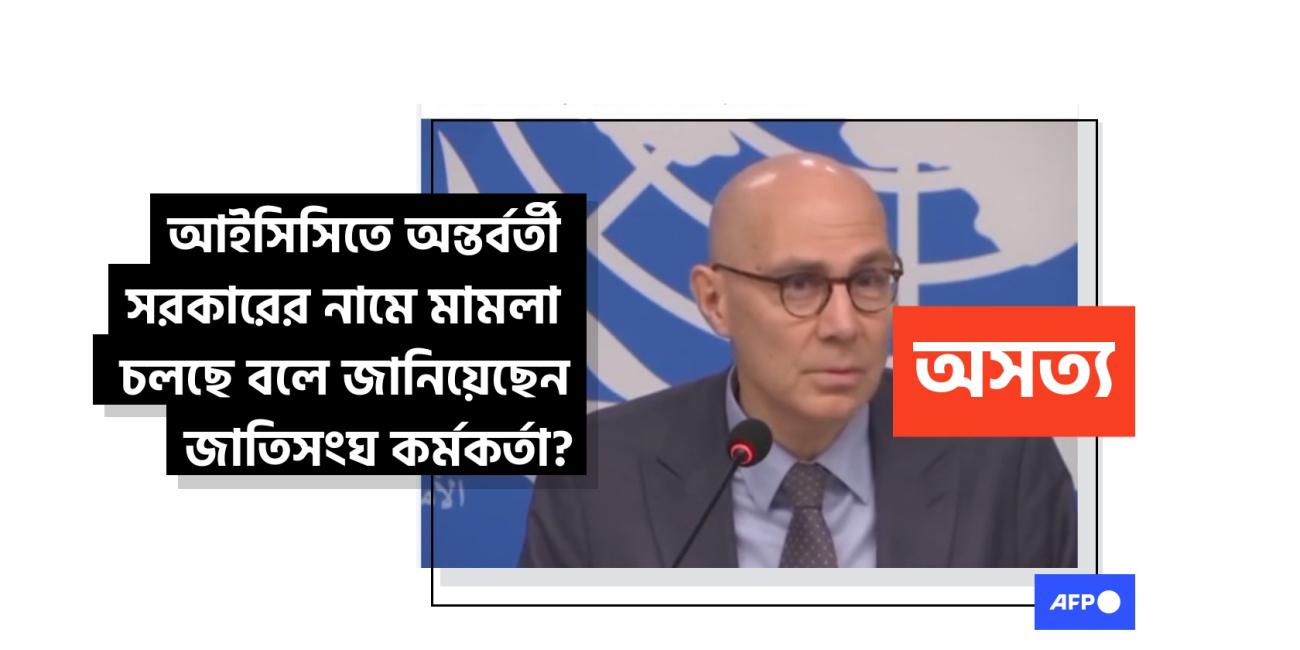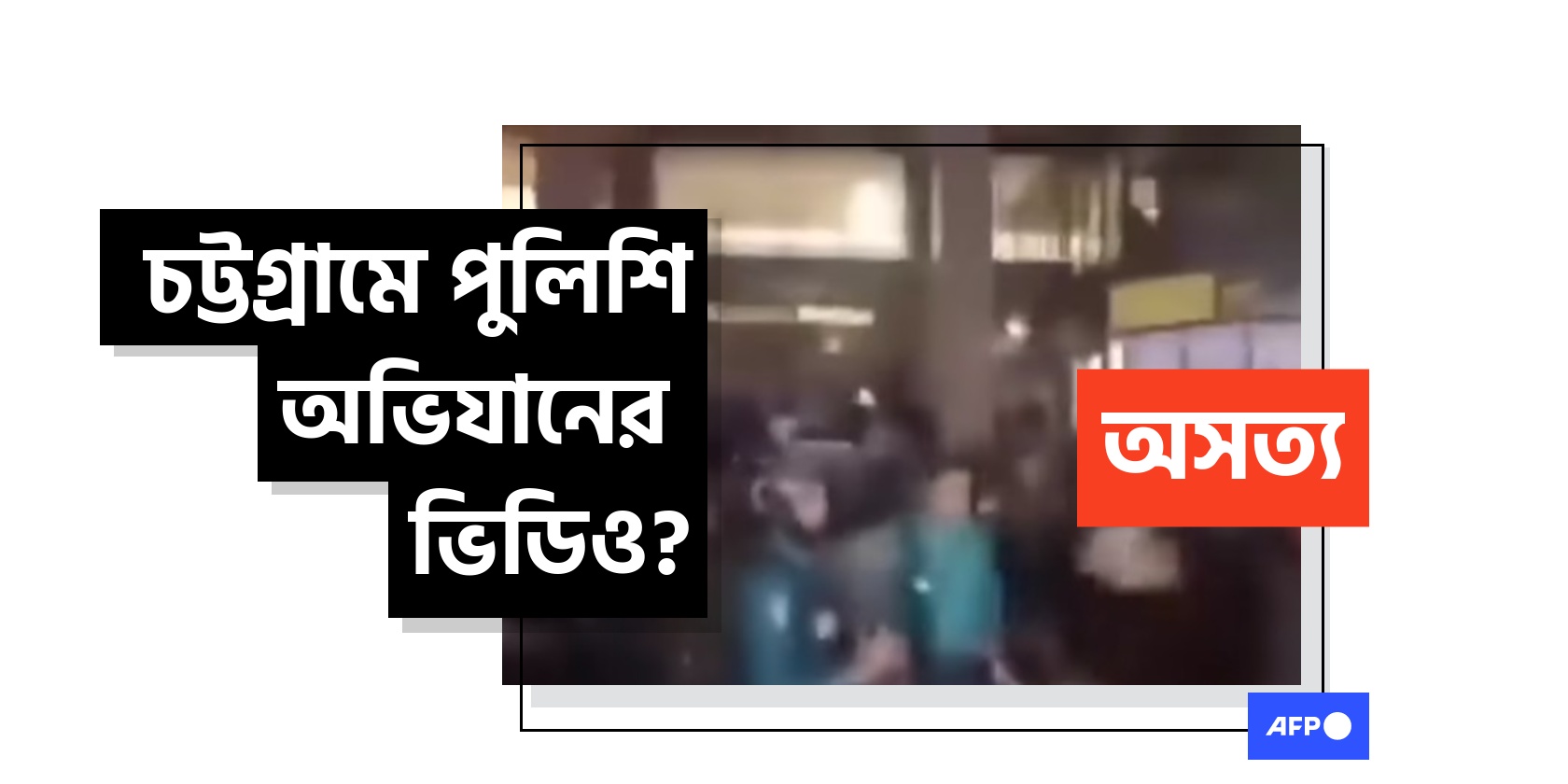
ঢাকার পুরনো সংঘাতের ভিডিওকে সম্প্রতি হাটহাজারী মাদ্রাসায় অভিযান হিসেবে অসত্যভাবে প্রচার
- প্রকাশিত 16 সেপ্টেম্বর 2025, 09:48
- 2 এক্স মিনিটে পড়ুন
- লেখক: Rasheek MUJIB, এএফপি বাংলাদেশ
গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে ছড়ানো একটি ফেসবুক পোস্টের ক্যাপশনে বলা হয়, “এই মুহূর্তে পাকিস্তান থেকে আনা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রের সন্ধানে হাটহাজারী মাদ্রাসায় পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর অভিযান চলছে।”
এক মিনিটের অস্পষ্ট ভিডিওটিতে একদল লোক এবং পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষের চিত্র দেখা যায়।

এক শিক্ষার্থীকে লাঞ্ছনার অভিযোগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদরে সাথে পাশ্ববর্তী গ্রামবাসীর মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর, পোস্টটি ফেসবুকে অন্যত্র শেয়ার করা হয়। সংঘর্ষে কয়েকদিন ধরে ক্লাস ব্যাহত হয় এবং শতাধিক আহতের ঘটনা ঘটে(আর্কাইভ লিংক)।
পোস্টের মন্তব্য থেকে মনে হচ্ছে অনেকেই অসত্য দাবিটি বিশ্বাস করেছেন।
একজন মন্তব্য করেন, “অস্ত্র বহনও সহজ হয়েছে। তাই সহজে যেকোন স্থানে নেয়া যায়। বড় প্রমাণ মাদ্রাসায় অস্ত্র অভিযান।”
অন্য একজন লিখেন, “বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু তদন্ত করে অস্ত্র উদ্ধার অভিজান চালিয়ে অস্ত্র মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করা হোক।”
ডাকসু নির্বাচনের সময় সংঘর্ষের ঘটনা হিসেবে ভিডিও অন্য আরেকটি ফেসবুক পোস্টে অসত্যভাবে ছড়ানো হয়।
কিফ্রেম নিয়ে গুগলে রিভার্স ইমেজ সার্চে ২৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে নাটশেল টুডে-র একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ভিডিওটি পাওয়া যায়(আর্কাইভ লিংক)।
ভিডিওটির ক্যাপশনে বলা হয়, “আজ কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো অফিসের সামনে।”
সেই সময় বিক্ষোভকারীরা প্রথম আলোর কার্যালয়ের বাইরে জড়ো হয়ে পত্রিকাটি বন্ধ করার দাবি জানায়। বিক্ষোভকারীরা ইট ছুঁড়ে মারার পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাঁদানে গ্যাস এবং সাউন্ড গ্রেনেড দিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে (আর্কাইভ লিংক)।
রিপোর্টারস ওইদাউট বর্ডারসের তথ্যমতে, সংবাদপত্রটি প্রতিবেশী ভারতের অর্থায়নে পরিচালিত এবং ধর্মনিরপেক্ষতা, এলজিবিটিকিউ প্লাস মানুষের অধিকার এবং নারী মুক্তির মতো ইসলামবিরোধী আদর্শ প্রচার করেছে বলে বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেছে (আর্কাইভ লিংক)।

ভিডিওটি ২৫ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে ইউটিউবেও প্রকাশিত হয়েছে(আর্কাইভ লিংক)।
অন্যান্য স্থানীয় সংবাদমাধ্যমও ভিন্ন কোণ থেকে তোলা একই রকম ফুটেজসহ ঘটনাটি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে(আর্কাইভ লিংক এখানে এবং এখানে)।
অসত্যভাবে ছড়ানো ভিডিওটিতে দৃশ্যমান ভবনের নাম এবং একটি এটিএম বুথসহ কিছু উপাদানের সাথে ঢাকার কারওয়ান বাজারের গুগল ম্যাপের স্ট্রিট ভিউয়ের মিল পাওয়া যায় (আর্কাইভ লিংক)।

এএফপি এর আগেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ঘিরে ছড়ানো অন্যান্য অপতথ্য খণ্ডন করেছে।
কপিরাইট © এএফপি ২০১৭-২০২৬। এই কন্টেন্টের যেকোন বানিজ্যিক ব্যবহারের জন্য অনুমতি নেয়া বাধ্যতামূলক। বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।
এমন কোনো কন্টেন্ট আছে যা আপনি এএফপি’কে দিয়ে ফ্যাক্ট চেক করাতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ